পশ্চিম থেকে ধার করা ট্রান্সবিদ্বেষী সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত
ট্রান্সফোবিয়া ও কুইরোফোবিয়ার যে ধারা বাংলাদেশে চলছে তা মূলত পশ্চিমা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতিফলন। অন্যদিকে যৌন ও লিঙ্গীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার ইতিহাস এ দেশের সমাজে বহু পুরনো।
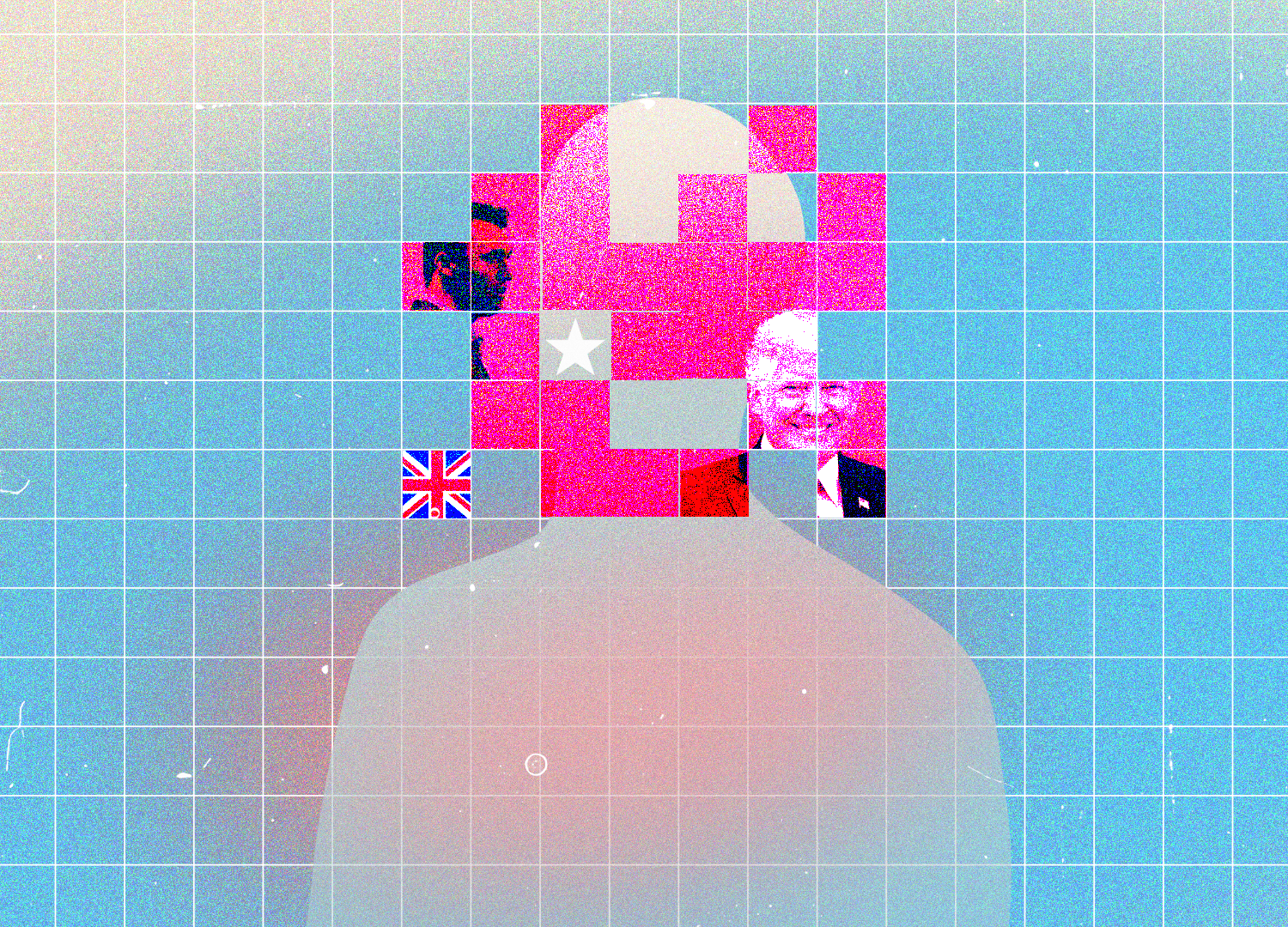
গত দশকে বাংলাদেশে প্রচলিত দ্বৈত লিঙ্গ ধারণার বাইরে যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংসতা ও হয়রানি বেড়েছে, যেখানে বিশেষভাবে বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডাররা, অর্থাৎ যাদের লিঙ্গ-পরিচয় জন্মের সময় নির্ধারিত যৌনতার সঙ্গে মেলে না। আগ্রাসী চিকিৎসা পদ্ধতি ও দেহগত স্বাধীনতা সম্পর্কে সেকেলে ধারণার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণে অব্যবস্থাপূর্ণ নীতির পাশাপাশি বেড়েছে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রকাশ্যে খারিজ করে দেওয়া, ডক্সিং বা হয়রানি করা এবং সমন্বিতভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান ও মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ট্রান্সফোবিয়া চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস পশ্চিমা বিশ্বের কাছে নিজের উদার ভাবমূর্তি বজায় রাখতে যখন-তখন সহমর্মিতার ভান করেন, কিন্তু বাংলাদেশের ভেতরে বাস্তবে কিছুই করেন না। এই ইস্যুতে ইউনুস ও তার উপদেষ্টাদের নীরবতা কার্যত রাষ্ট্র-সমর্থিত ঘৃণাচর্চার সমান, যা নিয়ে পশ্চিমা নবউদারবাদী সাম্রাজ্যবাদ গর্ব করতে পারে।
জনপ্রিয় বয়ান হচ্ছে— ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী পরিচয় নাকি বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি এক অবমাননা। সমাজের তথাকথিত সচেতন নাগরিকেরা দাবি করেন, তারা পশ্চিমা নবউদারবাদী সাম্রাজ্যবাদের “নৈতিক অধঃপতন” ঠেকিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা করছেন। এভাবে নাগরিকদের মৌলিক নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে প্রশ্নগুলো সমাজে এক নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে— কে আসলে “বাংলাদেশি সমাজের অংশ” হিসেবে স্বীকৃতি পাবে?
কিন্তু ট্রান্সফোব তথা ট্রান্সবিদ্বেষীরা যখন জনসাধারণকে বোঝাতে চায় যে, তারা কেবল “বিদেশি আগ্রাসন” থেকে স্থানীয় মূল্যবোধ রক্ষা করছে, তখন তাদের কৌশল দেখলে বোঝা যায় যে, আদতে এটি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে যা ঘটছে তারই অশুভ প্রতিফলন, যেগুলো নিজেরাই তথাকথিত অনৈতিকতার উৎস। ডেডনেমিং (লিঙ্গ বদলের অংশ হিসেবে নাম পরিবর্তন সত্ত্বেও ট্রান্সজেন্ডারদের জন্মের সময় দেওয়া নামে ডাকা) থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিদ্বেষ পর্যন্ত সমস্ত বিদ্বেষমূলক রূপ ও যুক্তি আসলে তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য।
শতাব্দীর শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দুটো দেশই অপ্রতিরোধ্যভাবে রক্ষণশীল ডানপন্থার দিকে সরে গেছে। ২০১০-এর দশকে আদালতের কিছু সিদ্ধান্তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছিল, তা ভেস্তে গেছে বিষাক্ত সামাজিক বাগাড়ম্বরের নিচে। এই বাগড়ম্বর ঘৃণাপূর্ণ অপরাধকে উসকে দিয়েছে, রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সংখ্যালঘুদের নিয়মিতভাবে অমানবিক করে তুলছেন কোনোরকম শাস্তি ছাড়াই। আর সাম্প্রতিক আদালতের মামলাগুলো বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের আইনি সুরক্ষা দিচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডার, নন-বাইনারি ও লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। শুধু যুক্তরাজ্যেই ট্রান্সফোবিক ঘৃণাজনিত অপরাধের সংখ্যা ২০১১–২০১২ সালে ৩১৩ থেকে বেড়ে ২০২৩–২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৪,৭৮০-তে। এগুলো কেবল নথিভুক্ত অপরাধ, অর্থাৎ ভুক্তভোগীকে তা রিপোর্ট করতে হয়েছে, যা একটি প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুইয়ারফোবিক দেশে বিরল ঘটনা। সন্দেহাতীতভাবে এইসব অপরাধের পিছনে ট্রান্সফোবিয়াই মূল প্রেরণা।
এই সহিংসতাকে জ্বালানি দিচ্ছে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বিশ্লেষকদের আনন্দিত ব্যবহার, যেখানে কুইয়ার সম্প্রদায়কে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি এক বন্দুকধারী কর্তৃক হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার হামলাকারীকে ট্রান্সজেন্ডার সন্দেহ করা হয়। এটা শোনার পর দেশজুড়ে গণমাধ্যমে আলোচনায় উঠল যে, সব লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের নাগরিক অধিকার সীমিত করা উচিত কি না। হোয়াইট হাউস ও বিচার বিভাগ এমন আইন খুঁজতে শুরু করেছে, যা ট্রান্সজেন্ডারদের অস্ত্র রাখার অধিকার সীমিত করতে পারে। ব্যাপারটি রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভাবার এক চমকপ্রদ উদাহরণ। অথচ ২০২৫ সালে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আরও ২৯৭টি বন্দুক হামলার ঘটেছে, যেগুলোর কোনোটি ট্রান্সজেন্ডার হামলাকারী দ্বারা ঘটেনি। চার্লি কার্ক ঘটনার পর একইভাবে ট্রান্স-বিরোধী ঘৃণা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয় হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশের পর। অবশ্য কিছু গণমাধ্যম এখনো খুঁজছে, তার কোনো ট্রান্সজেন্ডার বন্ধু ছিল কি না।
যুক্তরাজ্যে বিশাল অংশের উদ্বেগ ও অস্বাস্থ্যকর মনোযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রান্সজেন্ডাররা টয়লেট ব্যবহারের করছেন কি-না। এটি আসলে সেখানকার প্রতিদিনের ট্রান্সফোবিয়ার সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ। সমতা ও মানবাধিকার কমিশন (ইএইচআরসি), স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা মন্ত্রণালয়, ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি ও বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, শিক্ষাগত অধিকার সংগঠন এবং অসংখ্য তথাকথিত জেন্ডার-ক্রিটিক্যাল কর্মী (যাদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশের অভিজাত মহলে জনপ্রিয় উদার ব্যক্তিত্ব হিসেবে গৃহীত, যেমন জে. কে. রাউলিং), এরা সবাই মিলে দেশটির ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা, জনসমাগমস্থলে প্রবেশাধিকার, মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতাসহ সকল ক্ষেত্রেই অধিকার খর্ব করে ট্রান্সজেন্ডারদের এমনকি টিকে থাকাও অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে। একইসঙ্গে ট্রান্সফোবিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডকে ক্রমশ সুরক্ষিত করা হচ্ছে “মতপ্রকাশের অধিকার” বা “অজনপ্রিয় মতামত প্রকাশের সাহসী অধিকার” হিসেবে, যা এমন এক বয়ান তৈরি করছে যেখানে ট্রান্সফোবরা নাকি শুধু কথা বলছে না, বরং সামাজিক বুনন রক্ষায় সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে।
এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা লক্ষ্যবস্তু করছে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে, যারা যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৫৫% (সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী) এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১% (আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী)। শত হলেও, সংখ্যালঘুরাই আসলে সবচেয়ে ভালো বলির পাঁঠা হয়। বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের ওপর যে বৈষম্যমূলক ও সুযোগসন্ধানী আক্রমণ চলছে, সেটি একই ধরনের প্রক্রিয়ার প্রতিফলন এবং তা মোটেই সে বাংলাদেশি সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত নয়। ঐতিহাসিকভাবে, কুইয়ার পরিচয়ের অপরাধীকরণ হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। অথচ কুইয়ার পরিচয়ের অস্তিত্ব, গ্রহণযোগ্যতা, এমনকি উদ্যাপনও ইতিহাসে দেখা যায়। এমনকি ইসলামী প্রেক্ষাপটেও সেই ইতিহাস বাংলাদেশ বহন করে। প্রাক-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়াকে “কুইয়ার ইউটোপিয়া” বা ‘অবিষমকামীদের স্বর্গরাজ্য’ হিসেবে দেখানো ভুল হবে বটে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুইয়ার অভিব্যক্তির আরও বৈচিত্র্য ছিল, যা মূলত দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এই সম্প্রদায়গুলো অবশ্যই কষ্ট ও বৈষম্যের মুখোমুখি হতো, কিন্তু ব্রিটিশ দণ্ডবিধি চালু হওয়ার আগে তাদেরকে কোনো আইনি ও রাজনৈতিকভাবে “অন্য” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।
ব্রিটিশ দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭ প্রায়ই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু একইসঙ্গে আছে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট, যা পুরো সম্প্রদায়কে “অপরাধপ্রবণ” হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং এই আইনের আওতায় হিজড়া ও লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষদের গ্রেফতার ও বন্দি করা হতো শুধুমাত্র তাদের পরিচয়ের কারণে। এই আইনে হিজড়া ও লিঙ্গ-অসঙ্গত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং আজও দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এই সম্প্রদায়গুলোর (এবং কিছু জাতি ও আদিবাসী গোষ্ঠীর) আইনি বৈষম্যের ভিত্তি হয়ে আছে। লক্ষণীয়ভাবে, যেসব আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এখনো আধুনিক আইন ও পুলিশ কোড দ্বারা নিগৃহীত হয়, তাদের অনেকেরই কুইয়ার ও ট্রান্স অধিকারের প্রতি তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা সংহতি গড়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো মনে রাখা, ঔপনিবেশিক আমলে ধারা ৩৭৭-এর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল এক হিজড়ার বিরুদ্ধে— কোনো যৌন আচরণের জন্য নয় যে, তা আইন অনুযায়ী অপরাধ ছিল এবং এখনো আছে, বরং জনসমক্ষে গান গাওয়ার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঔপনিবেশিক আইনগুলো এবং তাদের আধুনিক সংস্করণ কখনোই শুধু তথাকথিত অনৈতিক আচরণ ঠেকানোর জন্য ছিল না, এগুলো ছিল সবসময়ই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও দমনের হাতিয়ার।
অতীতের রূপ আজও বর্তমানকে গঠন করছে। যেভাবে উপনিবেশবাদীরা বিভাজন সৃষ্টি করে শাসন কায়েম করেছিল, আজকের উত্তর-উপনিবেশবাদী জনতাবাদীরাও নিজেদের চিন্তার দারিদ্র্য ঢাকতে পশ্চিমের চরম-ডানপন্থীদের কাছ থেকে ধারণা ধার করে সেটাকে স্থানীয় বলে চালাচ্ছে। শ্বেত, খ্রিস্টান যুক্তি এখন ইসলামপন্থীদের মুখে “বাদামী, মুসলমান” যুক্তি হয়ে ফিরে আসছে— কোনো আত্মসমালোচনা ছাড়াই। অথচ তারা খ্রিস্টান ধর্মতন্ত্রের বিরোধিতা করে। তারা যে ধর্মীয় যুক্তি তুলে ধরে, তা ইউজেনিকস মতবাদের অনুসারী, যা পশ্চিমা ডানপন্থী মতাদর্শে পুনরুত্থান ঘটিয়েছে, যদিও তা বহু আগেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।
এই মানসিক দাসত্ব, যেখানে ট্রান্সফোবরা পশ্চিমের কাছ থেকে চিন্তাধারা ধার করে নিজেদের দেশকে ঘৃণার পথে ঠেলে দিচ্ছে— সেটাই নতুন সাম্রাজ্যবাদ। তাদের ইসলামী পরিচয়ের আবরণে এই ঘৃণা আরও ভয়ংকর, কারণ এতে ধর্মীয় আনুগত্যের আহ্বান ও ভয়ের মিশ্রণ ঘটে। আর এই ঘৃণার লক্ষ্য কেবল মানুষ নয়— সংস্কৃতি, শিল্প, আর সেই সব ঐতিহ্য যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশি ও বহুবর্ণ, যেগুলোকে দমন করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য।
বাংলাদেশি বিদ্বেষীরা পশ্চিমা ট্রান্সফোবিয়া হঠাৎ করে গ্রহণ করেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে যে রকম স্থানীয় সহযোগীদের ব্যবহার করেছিল, দক্ষিণ এশিয়ার কুইয়ারফোবিয়া ও নারীবিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তেমনই আধুনিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা খুশিমনে তাদের “স্বাধীনতার ব্র্যান্ড” অন্য দেশে রপ্তানি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নৈতিক অভিযাত্রা আসে খ্রিস্টান ইভানজেলিজমের মোড়কে, যা চালিকা শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ ভিক্টোরিয়ান খ্রিস্টধর্মকে প্রতিস্থাপন করেছে। অ্যালায়েন্স ডিফেন্ডিং ফ্রিডম (ADF) নামক সংগঠন— যার বৈশ্বিক বাজেট ১১.৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় সদর দপ্তর আছে, বিশেষভাবে কুইয়ার অধিকারের বিরোধী। তারা যুক্তরাষ্ট্রে ট্রান্সজেন্ডার তরুণদের স্বায়ত্তশাসন হ্রাসের লক্ষ্যে মামলায় অর্থায়ন করেছে, যুক্তরাজ্যের রাজনীতিবিদদের আইনি পরামর্শ দিয়েছে, যাতে ট্রান্স অধিকার অগ্রগতি ঠেকানো যায় এবং আফ্রিকায় অ্যান্টি-সোডোমি আইন চালুর প্রচেষ্টায় অর্থ ও লবিং সহায়তা দিয়েছে।
উগান্ডার কুখ্যাত ২০২৩ সালের অ্যান্টি-এলজিবিটিকিউ+ আইন মূলত ইভানজেলিকাল অর্থায়নে সম্ভব হয়েছে। একইভাবে ধারাবাহিকভাবে যুক্তরাজ্যের সরকারগুলো (কনজারভেটিভ ও লেবার উভয়ই) ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের সুরক্ষা দিতে পারে এমন কনভার্শন প্র্যাকটিসের ওপর নিঃশর্ত নিষেধাজ্ঞা আনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং এ বিষয়ে মার্কিন ইভানজেলিকাল উপদেষ্টাদের দিকনির্দেশনা নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেও তাদের প্রভাব বিশাল, যেখানে অনেক রিপাবলিকান রাজনীতিবিদ, এমনকি কিছু ডেমোক্র্যাটও এসব লবিং গ্রুপের সদস্য বা তাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত। যে লবিস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তিনজন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি বাছাইয়ে সহায়তা করেছিল (যারা সকলে ট্রান্স অধিকারবিরোধী), তিনি ছিলেন এডিএফ বোর্ডের সদস্য। রিপাবলিকান পার্টি ও হোয়াইট হাউস খুশিমনে বাইবেল ভুলভাবে উদ্ধৃত করে অ্যান্টি-এলজিবিটিকিউ+ নীতি প্রণয়নে। লক্ষণীয় যে, ইভানজেলিকাল অর্থায়ন কেবল তাদের নিজস্ব খ্রিস্টান ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে যে, অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গেও কাজ করতে তারা রাজি, যতক্ষণ না লক্ষ্য একই থাকে, অর্থাৎ “পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা।” এ কারণেই হয়তো অনলাইনে ইসলামপন্থা-প্রণোদিত ট্রান্সফোবিয়ার প্রবক্তাদের মধ্যে কিছু বাংলাদেশি প্রচারক, যারা ট্রান্স মানুষদের ডক্স করার বিপজ্জনক প্রচারণা চালায়। এরা রিপাবলিকান পার্টি ও সংশ্লিষ্ট ইভানজেলিকাল গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকাশ্য যোগসূত্র রাখে, যদিও তাদের ধর্মে কোনো মিল নেই।
এছাড়া মনে রাখা জরুরি, বাংলাদেশের বর্তমান ট্রান্সফোবিয়ার ধারা কেবল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর একমাত্র আক্রমণ নয়। পশ্চিমে যেমন ট্রান্সফোবরা বর্ণবাদ, হোমোফোবিয়া ও অ্যান্টি-অ্যাবরশন আন্দোলন সমর্থন করে, তেমনই বাংলাদেশে ট্রান্সফোবিয়া দেখা দিচ্ছে অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার দমনের পাশাপাশি। নারীবিদ্বেষী অপরাধ বাড়ছে, বিশেষত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু নারীদের বিরুদ্ধে। আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কারণ তাদের যথেষ্ট “বাংলাদেশি” বলে গণ্য করা হয় না, তাদের ভূমির মৌলিক অধিকার সত্ত্বেও। প্রান্তিক অধিকারের এই সর্বাত্মক আক্রমণ ভীতিকরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ২০১০-এর দশকের বাংলাদেশকে, যখন বহু সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতা ঘটেছিল, কিন্তু তারা সমর্থন বা জোট গড়তে পারেনি। বর্তমান পরিস্থিতি হয়তো কম সহিংস, তবে একই ধরনের “অন্যকরণ” ও ধর্মীয় আবরণের নিচে ডি-হিউম্যানাইজ করার পথ অনুসরণ করছে, যা পশ্চিমেও নিয়মিত ঘটেছে।
ট্রান্সজেন্ডার অস্তিত্ব, ইতিহাস ও উদ্যাপন বাংলাদেশের নিজস্ব এবং অবিসংবাদিত; যেমন অবিসংবাদিত হলো যে, এটির দমন সাম্রাজ্যবাদের ফসল। ট্রান্সফোবিয়াকে ন্যায্যতা দেওয়ার যে আইন, তা খ্রিস্টান নৈতিক পুলিশিং থেকে ইসলামপন্থায় ঠাঁই পেয়েছে; আর ট্রান্সফোবিয়া ছড়ানোর যে আধুনিক অর্থায়ন ও কৌশল, তা এসেছে মার্কিন ইভানজেলিজম থেকে। যদি বাংলাদেশের ট্রান্সফোবদের লক্ষ্য সত্যিই হয় পশ্চিমা প্রভাব মুছে দেওয়া হয়, তবে তাদের উচিত নিজেদের সংস্কৃতির ইতিহাসের দিকে তাকানো। হয়তো তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, যেসব অত্যাচারীদের তারা থামাতে চায়, আদতে ওরা নিজেরাই তা।●
ইবতিশাম আহমেদ একজন বাংলাদেশী একাডেমিশিয়ান, যিনি ইউটোপিয়ানিজম, বিউপনিবেশিক ইতিহাস এবং কুইয়ার তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ।